বিশ্ব রাজনীতির নিয়ন্ত্রণকারী আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনকে ঘিরে প্রতি চার বছর অন্তর অন্তর দেশ-বিদেশের সব শ্রেণির মানুষের মাঝে ব্যাপক আগ্রহ ও কৌতূহলের জন্ম নেয়, তবে কৌতূহল সৃষ্টি নিছক কোন কারণে নয় বরং একাধিক কারণেই মানুষের মাঝে এত আগ্রহ তৈরি হয়।
প্রথমত- আমরা লক্ষ্য করছি, ১৯৯০ -এরপর থেকে আমেরিকা এখন পৃথিবীর একমাত্র পরাশক্তি, যদিও ইদানীং চীন ও রাশিয়া নতুন করে তাদের শক্তিমত্তার জানান দিচ্ছে।
দ্বিতীয়ত- সে দেশের অর্থনীতি মানে কল্পনাতীত এক বিশাল কর্মযজ্ঞ! প্রতি বছর সেখানে সৃষ্টি হয় প্রায় ১৭ লাখ কোটি ডলারের সম্পদ, যা কিনা সারা দুনিয়ার প্রায় চার ভাগের এক ভাগ।
তৃতীয়ত- দেশ ও সভ্যতা হিসেবে খুব প্রাচীন না হলেও আমেরিকার সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্রচর্চার ইতিহাস প্রায় আড়াই শ’ বছরের।
অষ্টাদশ শতাব্দীর মাঝামাঝি ভারতবাসীরা যখন পরাধীন হয়, তার কাছাকাছি সময়ে আমেরিকা স্বাধীন হয়। এরপর থেকে মার্কিন জনগণ নিরবচ্ছিন্নভাবে তাদের সার্বভৌমত্ব ও গণতন্ত্র চর্চা করে আসছে। তবে তাদের জাতীয় জীবনে এর চেয়েও শক্তিশালী দিক হলো ১৮৬০ সালের গৃহযুদ্ধের পর সে দেশে তেমন বড় ধরনের কোনো রাজনৈতিক সঙ্কট দেখা দেয়নি। রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার দিক থেকে আমেরিকা পৃথিবীর বুকে একটা আদর্শ উদাহরণও বটে। মার্কিন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতার কারণ হল অন্যান্য দেশের মত এখানকার নির্বাচন ব্যবস্থা নয়। এখানকার জনগণ আমাদের মত নির্বাচন নিয়ে এত মাথা ঘামায় না। কোন সরকারের অধীনে, কোন কমিশনের হেফাজতে, কোন তারিখে, কিভাবে নির্বাচন হবে, এ নিয়ে আমেরিকার জনগণের কোনো মাথাব্যথা নেই। নির্বাচনের দিন-তারিখ সাংবিধানিকভাবে অনেক আগে থেকেই নির্ধারিত রয়েছে। প্রেসিডেন্টের মেয়াদের চতুর্থ বছরের নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার হলো নির্বাচনের দিন। তবে মাসের এক তারিখ যদি মঙ্গলবার হয়, সেক্ষেত্রে নির্বাচন হবে নভেম্বরের দ্বিতীয় মঙ্গলবারে। অর্থাৎ মাসের প্রথম দিন কোনো অবস্থাতেই নির্বাচন হতে পারবে না। মার্কিন রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা এতই পাকাপোক্ত যে, এখনই বলে দেয়া যায় কোন দূর্ঘটনা না ঘটলে ১০০ বছর পর কোন দিন, কোন তারিখ, কী বারে, কিভাবে সে দেশের নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে।
আমেরিকার নির্বাচন পদ্ধতি
বিশ্বের বুকে সুপার পাওয়ার রাষ্ট্র হিসেবে খ্যাত আমেরিকার নির্বাচন ব্যবস্থা অনেক জটিল। অন্যান্য দেশের মত এদেশের নির্বাচন পরিচালিত হয় না। গণতন্ত্রের ধারক বাহক হিসেবে নিজেকে উপস্থাপন করলেও খোদ নিজ দেশেই এ নির্বাচন নিয়ে নানা কথা রয়েছে। মার্কিন নির্বাচন প্রতি চার বছর পর পর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে। আর দেশটির প্রধান দুই দল থেকে প্রার্থী বাছাই করা হয়। ১৮৪৫ সাল থেকে নভেম্বর মাসের প্রথম মঙ্গলবার এই নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়ে আসছে। নির্বাচনে প্রার্থীদের যোগ্যতা বাছাইয়ে ৩টি শর্ত মানতে হয়। এক, যুক্তরাষ্ট্রের নাগরিক হতে হবে। দুই, ৩৫ বছরের বেশি বয়সী হতে হবে এবং তিন, ১৪ বছর যুক্তরাষ্ট্রের স্থায়ী হতে হবে। মার্কিন নির্বাচন ব্যবস্থায় ভোটের রয়েছে বিচিত্র সমাহার। কেননা কোন প্রার্থী সাধারণ জনগণের সর্বোচ্চ ভোট পেলেও সে প্রেসিডেন্ট নাও হতে পারে, যদি না সে ইলেকটোরাল ভোট বেশি না পায় অর্থাৎ এখানে সারাদেশ মিলিয়ে বেশি ভোট পাওয়া প্রার্থীই যে নিশ্চিত বিজয়ী হবেন এমনটা নয় বরং তাকে আসলে জিততে হবে রাজ্যগুলোর ইলেকটোরাল ভোটে। আমেরিকার প্রতিটি রাজ্যের জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে ইলেকটোরাল ভোট নির্ধারিত রয়েছে। একটি রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি ভোট পাবেন, সেই রাজ্যের সকল ইলেকটোরাল ভোটই তার হয়ে যাবে। দেশটিতে মোট ইলেকটোরাল ভোটের সংখ্যা ৫৩৮টি। যে প্রার্থী মোট ভোটের ২৭০ পার করবেন, তিনিই বিজয়ী হিসেবে গণ্য হবেন।
তবে আমেরিকাতে যে নির্বাচনী রেওয়াজ গড়ে উঠেছে, তাতে দেখা যায়, বেশির ভাগ রাজ্য একই দলকে জিতিয়ে আসছে দীর্ঘ দিন ধরে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া, নিউইয়র্কের বাসিন্দারা ডেমোক্রেটিক পার্টিকে জেতাচ্ছে আজ প্রায় ২০ বছর ধরে; ঠিক তেমনই টেক্সাস, লুইজিয়ানা, টেনেসির বাসিন্দারা যুগ যুগ ধরে রিপাবলিকানদের ভোট দিয়ে বিজয়ী করে আসছে। ফলে বিজয়ী হওয়ার জন্য হাতে গোনা কিছু রাজ্যে জয়লাভ করতে দু দলের প্রার্থীকে ব্যাপক দৌড়ঝাপ করতে হয়। মার্কিন রাজনীতির ভাষায় যাকে বলা হয় ব্যাটেলগ্রাউন্ড স্টেটস। এ ধরনের রাজ্যগুলো হল, ফ্লোরিডা (২৯ টি ইলেকটোরাল ভোট), পেনসিলভানিয়া (২০), নিউ হ্যাম্পশায়ার (৪), নেভাডা (৬), ওহাইয়ো (১৮), আইওয়া (৬), নর্থ ক্যারোলাইনা (১৫), কলোরাডো (৯) ও নিউমেক্সিকো (৫)।
আমেরিকায় রয়েছে মোট পঞ্চাশটি স্টেট আর একটি ফেডারাল ডিস্ট্রিক্ট তথা দেশের রাজধানী ওয়াশিংটন ডিসি। জনসংখ্যার ভিত্তিতে সব স্টেট ও রাজধানীর জন্য নির্ধারিত রয়েছে আলাদা আলাদা ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা। দেশটির ক্যালিফোর্নিয়া রাজ্যে ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা সবচেয়ে বেশি তথা পঞ্চান্নটি। এরপরের অবস্থানেই রয়েছে টেক্সাস, ফ্লোরিডা, নিউইয়র্ক। নির্বাচনের নীতি অনুযায়ী জনসংখ্যা যেমনই হোক না কেন স্টেটগুলির জন্য কমপক্ষে তিনটি করে ইলেকটোরাল ভোট বরাদ্দ রাখতেই হবে। এজন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে উইনার-টেক-অল নীতি মেনে চলা হয়। যার মানে হল যে রাজ্যে যে প্রার্থী সবচেয়ে বেশি মানুষের ভোট পাবেন, সেই স্টেটের সব ইলেকটোরাল ভোট তার হয়ে যাবে। আমেরিকার ভোটারদের ভোটের মূল্য বড় স্টেটগুলির তুলনায় ছোট স্টেটগুলিতে বেশি। যেমন মন্টানার জনসংখ্যা দশ লাখ। ওইয়োমিংয়ে বাস করেন ছয় লাখ মানুষ। কিন্তু, দুটি স্টেটেরই ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যা তিন। নির্বাচনে ছোট স্টেটগুলি যাতে গুরুত্ব না হারায় সে জন্যই মূলত এই ব্যবস্থা। সাধারণ মানুষের ভোট বেশি পেয়েও ইলেকটোরাল ভোট পদ্ধতির কারণে প্রেসিডেন্ট হতে পারেননি, আমেরিকায় এমন বহু উদাহরণ রয়েছে। চলতি ২০১৬ সালের নির্বাচন ছাড়াও ২০০০ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে ডেমোক্রেট প্রার্থী আল গোর পান ৪৮.৪% ভোট। রিপাবলিকান প্রার্থী জর্জ বুশ তাঁর চেয়ে কম ৪৭.৯% পপুলার ভোট পেয়েও ইলেকটোরাল ভোট সংখ্যার হিসাবে আল গোরকে টেক্কা দিয়ে প্রেসিডেন্ট হয়ে যান। এমনিভাবে ১৮৮৮ এবং ১৮৭৬ সালেও পপুলার ভোটে পিছিয়ে থেকেও আমেরিকার প্রেসিডেন্ট হওয়ার ইতিহাস রয়েছে।
নির্বাচনের দশ মাস পূর্ব থেকেই প্রেসিডেন্ট পদে প্রার্থী বাছাইয়ের প্রক্রিয়া শুরু হয়ে যায়। এ প্রক্রিয়া বড়ই বিচিত্র, দীর্ঘ, ব্যয়বহুল ও জটিল। বাছাই প্রক্রিয়া আরম্ভ হয় আইওয়া পার্টি কোকাসের মধ্য দিয়ে এবং শেষ হয় নির্বাচনের মাস দুয়েক আগে পার্টি কনভেনশনে, চূড়ান্ত মনোনয়নের মাধ্যমে। প্রার্থী বাছাইয়ের দায়িত্ব সংশ্লিষ্ট পার্টির ডেলিগেটদের ওপর ন্যস্ত থাকে। কোন প্রার্থীর পক্ষে কত ডেলিগেট, সেটা বোঝা যায় বাছাইপর্বে রাজ্যে রাজ্যে পার্টি কোকাস এবং প্রাইমারির মাধ্যমে, আর তাই এসব ছোট ছোট নির্বাচনকে ঘিরেও বিশ্বব্যাপী ব্যাপক উত্তেজনা দেখা যায়। এ বাছাইয়ের কাজ সব রাজ্যে একই পদ্ধতিতে হয় না বরং একেক রাজ্যের একেক নিয়ম। কোনো রাজ্যে পার্টির সদস্যরা কোকাসে ভোট অথবা আলাপ আলোচনার মাধ্যমে ঠিক করেন কোন প্রার্থীর পক্ষে কতজন ডেলিগেট; কোনো রাজ্যে সাধারণ ভোটাররা ভোটের মাধ্যমে ঠিক করেন কে কতজন ডেলিগেটের আস্থা পেলেন। এ নিয়মের সুযোগ নিয়ে কখনো কখনো এক দলের ভোটার অন্য দলের দুর্বল প্রার্থীকে ভোট দেয়, যাতে তিনি মনোনয়ন পেলে তার দলের, তার প্রিয় প্রার্থী আসল নির্বাচনে সহজে জিততে পারেন। এটাকে বলা হয় গড়হশবু ইঁংরহবংং। তবে প্রাইমারিতে একজন ভোটার শুধু এক দলের প্রার্থী বাছাইয়ে অংশ নিতে পারেন, উভয় দলের নয়। বাছাই পর্ব শেষ হলে ডেলিগেটরা পার্টির জাতীয় কনভেনশনে গিয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে ভোটের মাধ্যমে দলীয় মনোনয়ন চূড়ান্ত করেন। ডেলিগেটদের সংখ্যা একেক পার্টিতে একেক রকম এবং বছর বছর এর হেরফেরও হতে পারে। ২০১৬ সালের নির্বাচনে রিপাবলিকানদের মোট ডেলিগেট সংখ্যা ছিল ২৪৭২। আর চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য দরকার ছিল কমপক্ষে ১২৩৭। অপরদিকে ডেমোক্রেটদের মোট ডেলিগেট সংখ্যা ছিল ৪৭৬৩। আর নমিনেশনের জন্য দরকার ছিল কমপক্ষে ২৩৮২ জনের ভোট। বাছাই পর্বে পোর্টোরিকো, ভার্জিন আয়ারল্যান্ডস, আমেরিকান সেমোয়া এবং অন্যান্য মার্কিন টেরিটরির জনগণ অংশ নিলেও মূল নির্বাচনে তাদের কোনো ভোটাধিকার নেই, কারণ তারা ফেডারেল আয়করের আওতার বাইরে।
যেহেতু প্রতি লিপইয়ারে নির্বাচন হয়, তাই প্রেসিডেন্টের শাসনকালের মেয়াদ মাত্র চার বছরের এবং তিনি পরপর দুই বারের বেশি প্রার্থীও হতে পারেন না। এ নির্বাচনে জাতীয়ভাবে এবং দুনিয়াব্যাপী যদিও আলোচনায় থাকেন শুধু প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা, তথাপি একই দিনে মার্কিন ভোটাররা আরো অনেক পদে প্রার্থী নির্বাচন করে থাকেন- যেমন কংগ্রেস প্রতিনিধি পরিষদের ৪৩৫ জন সদস্য এবং একাধিক মেয়াদোত্তীর্ণ সিনেটর, স্টেট লেজিসলেটর, স্টেট সিনেটর, স্টেট গভর্নর ইত্যাদি। এ ছাড়াও বিভিন্ন রাজ্যে এবং কাউন্টিতে নানান ধরনের রাজনৈতিক, সামাজিক, আইনি ও রাজস্ব বিষয়ক বিতর্কিত ইস্যুর ওপর গণভোট নেয়া হয়। তবে মার্কিন কেন্দ্রীয় প্রতিনিধি পরিষদের সদস্যদের মেয়াদ মাত্র দুই বছরের। তাই তারা প্রতি দুই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের মাঝখানে আরেকবার জনগণের ম্যান্ডেট নিতে বাধ্য। ওই নির্বাচনকে বলে গরফঃবৎস ঊষবপঃরড়হ। ফেডারেল সিনেটরদের মেয়াদ ছয় বছরের, তবে তাদের মেয়াদ পালাক্রমে এমনভাবে বিন্যাস করা যে, প্রতি দুই বছর অন্তর অন্তর কিছু না কিছু সিনেটরকে ছয় বছর পূর্ণ করে নির্বাচনের মাঠে নামতে হয়, স্টেট গভর্নরদের মেয়াদ চার বছরের এবং তাদেরও কাউকে না কাউকে মিডটার্ম ইলেকশন মোকাবেলা করতে হয়।
নির্বাচনের ঠিক কয়েক সপ্তাহ আগে উভয় প্রেসিডেন্ট প্রার্থী তার ভাইস প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীর (যাকে বলা হয় জঁহহরহমসধঃব) নাম ঘোষণা করেন। প্রেসিডেন্ট পদে যে জিতবেন তার ৎঁহহরহমসধঃব আপনা আপনিই জয়যুক্ত বলে বিবেচিত হন। প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন নভেম্বরের প্রথম দিকে, কিন্তু শপথ নিয়ে হোয়াইট হাউজের ওভাল অফিসে বসতে বসতে হয়ে যায় জানুয়ারির শেষ সপ্তাহ। তিনি এই আড়াই মাস সময় পান সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে তার গোটা প্রশাসনিক টিম সাজানোর জন্য। এ অন্তরবর্তী সময়ে বিদায়ী প্রেসিডেন্টকে বলা হয় খধসব উঁপশ প্রেসিডেন্ট। তিনি শুধু দৈনন্দিন রুটিন অনুযায়ী কাজ চালিয়ে যান, যেকোনো গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়ার আগে তাকে “প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট” এর পরামর্শ নিতে হয়। নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথেই ফেডারেল সিক্রেট সার্ভিসের নিরাপত্তারক্ষীরা “প্রেসিডেন্ট ইলেক্ট” এর ব্যক্তিগত ও পারিবারিক নিরাপত্তা নিশ্চিত করে থাকেন।
নির্বাচনে ফেথলেস ইলেক্টর বা বেঈমান ইলেক্টর এর পরিচয়
মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে যে স্টেটে যে দল যতগুলি ইলেকটোরাল ভোট লাভ করে, সেই দলের ততজন প্রতিনিধি আবার সরাসরি প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দেন। অর্থাৎ, কোন প্রার্থী যদি ২৭০টি ইলেকটোরাল ভোট পান তা হলে তাঁর দলের ২৭০ জন প্রতিনিধির দেওয়া সরাসরি ভোটে তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন। তবে চাইলে ইলেকটোরাল কলেজের কোনও দলীয় প্রতিনিধি নিজের দলের বদলে অন্য দলের প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীকে ভোট দিতে পারেন। এদের বলা হয় ফেথলেস ইলেক্টর বা বেঈমান ইলেক্টর। আমেরিকায় এরকম বেঈমানির একশো সাতান্নটি উদাহরণ আছে। তবে, তাতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ফলাফল বদলের নজির নেই।
মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট
ডিবেটের মাধ্যমেই মূলত নেতার যোগ্যতা, বিচক্ষণতা ও জ্ঞানের পরিধি পরিমাপ করা যায়। এরই সূত্র ধরে দীর্ঘ দিন যাবত মার্কিন প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেট চলে আসছে। মার্কিন ইতিহাসে এ ডিবেট খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সারাবিশ্ব তখন এ বির্তকের দিকে চোখ রাখেন। প্রেসিডেন্ট প্রার্থীদের মাঝে তিনটি এবং ভাইস প্রেসিডেন্ট প্রার্থীর মাঝে একটি ডিবেট অনুষ্ঠিত হয়। এর মাধ্যমে প্রার্থী টেলিভিশন বিতর্কে নিজেদের এজেন্ডা ও যুক্তি পেশ করেন। তবে ২০১৬ সালের মার্কিন নির্বাচনে হিলারি ও ট্রাম্পের জিবেট পরিণত হয়েছে ব্যক্তিগত কাদা ছোঁড়াছুড়িতে। কেননা মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন বিতর্কে এবার সৌজন্যের লেশমাত্র ছিল না। আমেরিকার বিতর্কের ইতিহাসে দেখা যায়, সর্বপ্রথম ১৮৫৮ সালে সিনেটর নির্বাচনে অ ডগলাসের সঙ্গে প্রথম প্রকাশ্যে বিতর্কে লড়েন আব্রাহাম লিঙ্কন। তবে ফ্রাঙ্কলিন ডি রুজভেল্ট দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় ১৯৪০ সালে ওয়েনডেল উইলকির সাথে বিতর্কের চ্যালেঞ্জ নিতে অস্বীকার করেন। মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ইতিহাসে বিতর্কের প্রথম প্রবেশ ঘটে ১৯৬০ সালে। শিকাগোর স্টুডিওতে রিপাবলিকান প্রার্থী রিচার্ড নিক্সনের সঙ্গে বিতর্কে অংশ নেন ডেমোক্রেট প্রার্থী জন এফ কেনেডি। এরপর থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সঙ্গে স্টুডিও বিতর্ক ওতপ্রোতভাবে জড়িত।
২০১৬ সালের বিতর্ক বিশ্লেষণ
প্রথম বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় ২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৬ নিউইয়র্কের হফস্ট্রা ইউনিভার্সিটিতে। এতে সিএনএন, ওআরসির জরিপে ট্রাম্পের চেয়ে হিলারি এগিয়ে ছিল। হিলারির জনসমর্থন ছিল শতকরা ৬২ ভাগ আর ট্রাম্পের জনসমর্থন শতকরা ২৭ ভাগ ছিল। দ্বিতীয় বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় ৯ অক্টোবর ২০১৬ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটিতে। এতেও দেখা যায়, সিএনএনের জরিপে হিলারির জনসমর্থন ছিল শতকরা ৫৭ ভাগ আর ট্রাম্পের জনসমর্থন শতকরা ৩৪ ভাগ ছিল। হিলারী আর ট্রাম্পের মাঝে সর্বশেষ বিতর্ক অনুষ্ঠিত হয় নিউইয়র্কের ইউনিভার্সিটি অব নাভাদাতে ১৯ অক্টোবর ২০১৬ । সর্বশেষ এ বিতর্কের ফলাফলেও দেখা যায়, সিএনএন ও ফক্স নিউজের জরিপে হিলারির জনসমর্থন ছিল শতকরা ৫২ ভাগ আর ট্রাম্পের জনসমর্থন ছিল শতকরা ৩৯ ভাগ। এভাবে সবগুলো বিতর্কের জরিপে এবিসি নিউজের জনমত জরিপ মতে ট্রাম্পকে পিছনে ফেলে হিলারি এগিয়ে যায়। হিলারির জনসমর্থন ছিল শতকরা ৫০ ভাগ আর ট্রাম্পের জনসমর্থন ছিল শতকরা ৩৮ ভাগ।
হিলারি ও ডোনাল্ট ট্রাম্পের বিতর্ক বিশ্লেষণে দেখা যায়, ট্রাম্প প্রচারে যত ঝড় তুলেছিলেন যুক্তির যুদ্ধে তার প্রতিফলন ঘটাতে পারেন নি। কিন্তু, ডিবেটে অ্যাডভান্টেজ পেতে কম চেষ্টা করেননি। নিউইয়র্কে ডিবেটের আগে বিল ক্লিন্টনের বিরুদ্ধে যৌন কেলেঙ্কারির পুরনো অভিযোগ উত্থাপন করেন । কিন্তু, এর মাধ্যমে মূলত তাঁর নিজের যৌন কেলেঙ্কারিগুলিই প্রকাশ্যে আসে। তার বিরুদ্ধে এ অভিযোগ আসার পর থেকেই তিনি ব্যক্তিগত আক্রমণ শুরু করেন। ১৯ অক্টোবর লাস ভেগাসের নেভাডায় তৃতীয় তথা শেষ প্রেসিডেন্সিয়াল ডিবেটে মিলিত হন হিলারি ও ট্রাম্প। এই বিতর্কে তাদের মাঝে সৌজন্যের লেশমাত্র ছিল না। প্রথাগত করমর্দন এড়িয়ে তারা সরাসরি মঞ্চে উঠে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাদের বিতর্ক গড়ায় কর সংস্কারের দিকে। হিলারি তখন আক্রমণ করেন ট্রাম্পের কোম্পানির আউটসোর্সিংকে। হিলারি ক্লিনটন শুরুতেই পুতিনের প্রসঙ্গ নিয়ে সমালোচনা করেন । ট্রাম্পকে পুতিনের হাতের পুতুল হিসেবে আখ্যায়িত করেন। আবার ট্রাম্প হিলারিকে নীচ মহিলা বলে গালিগালাজ করেন। তবে তৃতীয় বিতর্কের শেষে জনমত সমীক্ষায় ট্রাম্পের চেয়ে প্রায় ১২% সমর্থনে এগিয়ে ছিলেন হিলারি। কিন্তু, বিতর্কেই নির্বাচনের মীমাংসা হয়নি। হিলারির বিরুদ্ধে ই- মেইল বিতর্কে ঋইও এর তদন্ত শুরু হতেই হিলারির সমর্থনে ভাটা পড়তে থাকে। ফলে শেষ দিকের জনমত সমীক্ষায় হিলারি ক্লিনটন, ডোনাল্ড ট্রাম্পের চেয়ে মাত্র ৬% ভোটে এগিয়ে ছিলেন। কিন্তু ট্রাম্প শিবির ঋইও কে হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার শুরু করে। এ সুযোগে রিপাবলিকানরা প্রচার করে যে, হিলারি ভোটে জিতলে দেশে সাংবিধানিক সঙ্কট তৈরি হবে কেননা হিলারি ই-মেইল কেলেঙ্কারিতে জেলে যাবেন। এমতাবস্থায় হিলারির লোকেরাও পাল্টা প্রচারে লিপ্ত হয়, তারা প্রচার করে, ট্রাম্প মহিলাদের অসম্মান করেন, বর্ণবৈষম্যে উস্কানি দেন, তিনি যুদ্ধবাজ এমনকি রিপাবলিকানদের একটা বড় অংশও ট্রাম্পকে পছন্দ করেন না।
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ও ভাইস প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কয়েকটি বিচিত্র বৈশিষ্ট্য রয়েছে।
প্রথমত
এটা গণতান্ত্রিক হলেও প্রত্যক্ষ নয়। পপুলার ভোট যে যতই পান না কেন, মোট ৫৩৮ ইলেকটোরাল কলেজের মধ্যে কমপক্ষে ২৭০টি না পেলে নির্বাচিত হওয়া যায় না। এই ৫৩৮ টি ইলেকটোরাল ভোটের কারণে একজন প্রার্থী বেশি পপুলার ভোট পেয়েও নির্বাচনে হারতে পারেন। ২০০০ সালে জর্জ বুশ জুনিয়রের কাছে এভাবেই আল গোরের পরাজয় হয়েছিল। তদ্রুপভাবে ২০১৬ সালের নির্বাচনে হিলারি পপুলার ভোটে এগিয়ে থাকলেও ইলেকটোরাল ভোটে ট্রাম্পের কাছে পরাজয় বরণ করেন। হিলারি-ট্রাম্পের এই প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দেখা যায়, ডেমোক্রেট প্রার্থী হিলারি ক্লিনটন পপুলার ভোট পেয়েছেন ৬,০৫,১৫,২৬৪ (ছয় কোটি পাঁচ লাখ পনের হাজার দুইশত চৌষট্টিটি) যা মোট ভোটের ৪৭.৭%। পক্ষান্তরে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প পেয়েছেন ৬,০০,৮৫,৪৫৬ (ছয় কোটি পঁচাশি হাজার চারশত ছাপ্পান্নটি) যা মোট ভোটের ৪৭.৩%। অর্থাৎ হিলারি ক্লিনটন ৪,২৯,৮০৮ (চার লাখ ঊনত্রিশ হাজার আটশত আট ) বা ০.৪% ভোট বেশি পেয়েছেন। ভোটের এই ব্যবধান সত্ত্বেও নির্বাচনে জিতেছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প। আমেরিকার সংবিধানে এ পরোক্ষ নির্বাচন ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, ছোট-বড় সব অঙ্গরাজ্যের ক্ষমতায় ভারসাম্য বজায় রাখার জন্য। অন্যথায় প্রেসিডেন্ট যদি কেবল পপুলার ভোটে নির্বাচিত হতেন, তাহলে শুধু ক্যালিফোর্নিয়া, টেক্সাস, নিউইউয়র্ক, ওহাইও, ফ্লোরিডা, ইলিনয়, প্যাসিলভানিয়া ইত্যাদি কয়েকটা জনবহুল রাজ্যের দ্বারাই নির্বাচনের ফায়সালা হয়ে যেত। দেশের নির্বাচনে ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় ছোট ছোট বাকি রাজ্যগুলোর কোনো মূল্য থাকত না।
দ্বিতীয়ত
এটা জাতীয় নির্বাচন হলেও কোনো একক জাতীয় নিয়মের ভিত্তিতে এ নির্বাচন হয় না। প্রতিটি অঙ্গরাজ্য তার নিজস্ব নিয়ম ও আইনের ভিত্তিতে ভোটগ্রহণ কার্যক্রম পরিচালনা করে। পৃথিবীর অন্য কোনো দেশে এমনটি নেই বললেই চলে। মেইন ও নেব্রাস্কা ছাড়া বাকি সব ক’টি অঙ্গরাজ্যে যে প্রার্থী বেশির ভাগ পপুলার ভোট পান, সে রাজ্যে তার মনোনীত ইলেকটোরাল কলেজের সবাই জিতলেন বলে বিবেচিত হবে। পক্ষান্তরে প্রতিদ্বন্ধী পার্টির সব ইলেকটোরাল কলেজই পরাজিত বলে গণ্য হয়। মেইন এবং নেব্রাস্কার ক্ষেত্রে এ নিয়ম কাজ করে না কেননা ওই দুই রাজ্যে যে প্রার্থী পপুলার ভোটে জয় লাভ করেন, তিনি পান রাজ্যের দুই সিনেটরের বিপরীতে দুটো ইলেকটোরাল কলেজ, বাকিগুলো নির্ভর করে রাজ্যজুড়ে আনুপাতিক প্রাপ্ত ভোটের ওপর। অর্থাৎ যে প্রার্থী যে কয়টি কংগ্রেশনাল ডিস্ট্রিক্টে জিতেন, তিনি পান আরো ততটি ইলেকটোরাল কলেজ।
তৃতীয়ত
আমরা জানি আমেরিকার রাজনীতির নিয়ামক মূলত দুটো দল। রিপাবলিকান ও ডেমোক্রেটিক পার্টি। তবে সাম্প্রতিক নির্বাচনসমূহে ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকান দলের পাশাপাশি আরো দুটি দলের কিছুটা সরব অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। এর মধ্যে একটি দল হলো জিল স্টেইনের দ্য গ্রিন পার্টি ও অন্যটি গ্যারি জনসনের লিবার্টারিয়ান পার্টি। ২০১৬ সালের নির্বাচনের ব্যালট পেপারেও তাদের নাম ছিল। তারা জাতীয় পর্যায়ে তুলনামূলকভাবে অপরিচিত। এমনকি জনসন নিউ মেক্সিকো ও ড. জিল স্টেইন ম্যাসাচুসেটসের গভর্নর হলেও পার্টিগতভাবে যুক্তরাষ্ট্রে তাদের পরিচিতি কম। তাদের দলের নেই বড় কোনো তহবিল। যার অভাবে তারা বড় দুটি রাজনৈতিক দল ডেমোক্রেট ও রিপাবলিকানের সঙ্গে প্রচার-প্রচারণায় প্রতিযোগিতা করতে সক্ষম হয় না। পরিসংখ্যানে দেখা যায়, এবারের নির্বাচনে হিলারি ক্লিনটন ও ডোনাল্ড ট্রাম্প যথাক্রমে ৪৭.৭% ও ৪৭.৩% পপুলার ভোট পেয়েছেন। তারা উভয়ে পেয়েছেন মোট ভোটের ৯৫%। অবশিষ্ট ৫% ভোট অন্য দুটি দল তথা গ্রিন ও লিবার্টারিয়ান পার্টি ও স্বতন্ত্র প্রার্থীরা পেয়েছেন। তাদের মাত্র ০.০৪% ভোটই ব্যবধান গড়ে দিয়েছে ট্রাম্প ও হিলারির মধ্যে। আদর্শগতভাবে রিপাবলিকানরা কনজারভেটিভ, তারা করপোরেট আমেরিকা এবং সুপার ধনীদের স্বার্থই বেশি করে দেখেন, মিলিটারি ইন্ডাস্ট্রিয়াল কমপ্লেক্সের দোসর, কারণে-অকারণে তারা যুদ্ধ বাধাতে চান। অপরদিকে ডেমোক্রেটিক পার্টি লিবারেল, তারা প্লুরেলিজমে বিশ্বাস করেন, ইমিগ্র্যান্ট ও ছোট জাতিগোষ্ঠীর প্রতি সহানুভূতিশীল, গরিব ও মধ্যবিত্তদের স্বার্থের ব্যাপারেও অধিক যতœবান ও সংবেদনশীল। মার্কিন রাজনীতির আরেকটি চরিত্র হলো, তারা কেন্দ্রীয় নির্বাচনে এক দিকে ভোট দেয় আবার আঞ্চলিক নির্বাচনে ভোট দেয় অন্য দিকে। যেমন ক্যালিফোর্নিয়া একটি ব্লু-স্টেট, তারা প্রেসিডেন্সিয়াল ইলেকশনে চোখ বুজে ভোট দেয় ডেমোক্রেটিক পার্টিকে, আবার রাজ্য নির্বাচনে অনেক সময় গভর্নর বানায় রিপাবলিকান প্রার্থীকে।
চতুর্থত
বছর বছর একটু-আধটু পরিবর্তন হলেও প্রতি নির্বাচনে রেড, ব্লু এŸং টসআপ বা সুইং স্টেটের এক অদ্ভুত হিসাবের মাধ্যমে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফলাফল নির্ধারিত হয়। রেড স্টেট মানে রিপাবলিকান ম্যাজরিটি, ব্লু-স্টেট অর্থাৎ ডেমোক্রেটিক স্ট্রংহোল্ড এবং টসআপ স্টেট মানে উভয় দিকে যেতে পারে। সঙ্গত কারণেই ব্লু এবং রেড জোনে বলতে গেলে ক্যাম্পেইন হয়ই না। কারণ এতে কোনো লাভ নেই, এরা ঐতিহাসিকভাবে নিজ নিজ দলের বাঁধা ভোট। ঝুলন্ত কিংবা সুইং স্টেটগুলোতেই চলে দু’পক্ষের জোড়ালো ক্যাম্পেইন। এই সুইং স্টেটের মধ্যে বড় হলো তিনটি- পেনসিলভানিয়া, ওহাইও ও ফ্লোরিডা। বলা হয়ে থাকে, এ তিন রাজ্যের মধ্যে যে দুটো পান, তিনিই বিজয়ী হন। অর্থাৎ শেষ মুহূর্তে দুইপক্ষই তাদের পুরো প্রচারণা শক্তি নিয়োগ করে থাকেন এই তিন রাজ্যের মধ্যে। তবে এ তিন স্টেটে অনিশ্চয়তার কারণে অন্য ছোট ছোট সুইং স্টেটেও প্রচারণা চলে।
আমেরিকার সরকার পদ্ধতি
আমেরিকা ডেমোক্রেটিক রিপাবলিকান বা গণতান্ত্রিক প্রজাতন্ত্র হিসেবে পরিচিত। সেখানে ফেডারেল বা কেন্দ্রীয় সরকারের রয়েছে তিনটি বিভাগ। অঙ্গরাজ্যের সরকারগুলোরও রয়েছে অনুরূপ কাঠামো।
বিভাগ তিনটি হচ্ছে-
১. নির্বাহী বিভাগ : দেশ পরিচালনায় প্রেসিডেন্ট এবং বিভিন্ন বিভাগের ও কার্যালয়ের হাজার হাজার কর্মকর্তা-কর্মচারী এ বিভাগের দায়িত্ব পালন করেন। এই নির্বাহী বিভাগের মাধ্যমে কংগ্রেসে পাসকৃত আইন-কানুন বাস্তবায়ন করা হয়।
২. আইন বিভাগ : সিনেট ও হাউজ অব রিপ্রেজেনটেটিভস নিয়ে গঠিত এই বিভাগ। সমষ্টিগতভাবে এর নাম কংগ্রেস। কংগ্রেসের দায়িত্ব হল আইন প্রণয়ন করা।
৩. বিচার বিভাগ : সুপ্রিম কোর্টের নয় বিচারপতি ও নিম্ন আদালত নিয়ে গঠিত হয় এই বিভাগ। এই বিভাগ সংবিধান সংশ্লিষ্ট আইনের ব্যাখ্যা প্রদান করে থাকে।
আমেরিকার বিতর্কিত প্রেসিডেন্ট প্রার্থী
আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে বিভিন্ন বিষয় নিয়ে নির্বাচিত প্রার্থীরা অনেক সময় সমালোচনার শিকার হন। ২০১৬ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে রিপাবলিকান প্রার্থী ডোনাল্ড ট্রাম্প, নানা বিতর্ক আর কেলেঙ্কারিতে মানুষের আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছিলেন। তবে আমেরিকার ইতিহাসে এর আগেও এমন ঘটনা ঘটেছে। বিশ শতকের প্রতাপশালী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী জর্জ ওয়ালেসও বিতর্কিত হয়েছিলেন। তিনি চারবার প্রেসিডেন্ট পদে প্রতিদ্বন্ধিতা করেও জয়ী হতে পারেননি। আমেরিকার বর্ণবাদবিরোধী সময়গুলোয় তার বর্ণবাদী আচরণে তিনি বিতর্কিত হয়েছিলেন। ১৯৩৬ ও ১৯৪০ সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ছিলেন আর্ল ব্রাউডার। রাশিয়ান পাসপোর্ট গোপন করে রাশিয়ান এক গুপ্তচরকে বিয়ে করায় তিনি বিতর্কিত হন। এ ঘটনায় তার চার বছরের জেলও হয়েছিল। এমনিভাবে জন চার্লস ফ্রেমন্ট ছিলেন ১৮৭৮ সালের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী। রাজনৈতিক অভিজ্ঞতায় তিনি টাইম ম্যাগাজিনের প্রচ্ছদে জায়গা পেয়েছিলেন। কিন্তু অভিযোগ উঠে তিনি ও তার দলবল সিরেয়াসে অভিযানে পথ হারিয়ে ফেলেন। তখন অনাহারে বেঁচে থাকার তাগিদে নরমাংস ভক্ষণ করেন। নির্বাচনের আগেই বিষয়টি জনসম্মুখে চলে আসে। ফলে তিনি নির্বাচনে হেরে যান। এমনি করে গ্রোভার ক্লিভল্যান্ডও বিতর্কের বাইরে ছিলেন না। তিনি নাকি শিশুপ্রেমে জড়িয়ে পড়ে ছিলেন। পরবর্তীতে ধর্ষণের মতো অভিযোগ উঠে তার বিরুদ্ধে। এদের বাইরেও অনেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী বিতর্কিত হয়েছিলেন। বেরি গোল্ডওয়াটার, এগুন ভি ডেবস, হুয়ে পি লং, ভিক্টোরিয়া উডহুল, পেট জে বচ্চন, জর্জ ইডেন টেইলরের মতো অভিজ্ঞ রাজনীতিবিদও পার পাননি। ফলে তাদের নির্বাচনের ফলাফল পরাজয় ছাড়া আর কিছুই ছিল না। তবে ২০০৬ সালে উইকিলিকসের তথ্য ফাঁসের ঘটনায় সাবেক প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশ চরমভাবে বিতর্কিত হন। মার্কিন ইতিহাসে জর্জ বুশ ও নব নির্বাচিত প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ট ট্রাম্প সবচেয়ে বিতর্কিত ব্যক্তি হিসেবে বিবেচিত হন। (চলবে…)
সংকলন, সংযোজন ও পরিমার্জনে
কেন্দ্রীয় সভাপতি
ইসলামী শাসনতন্ত্র ছাত্র আন্দোলন


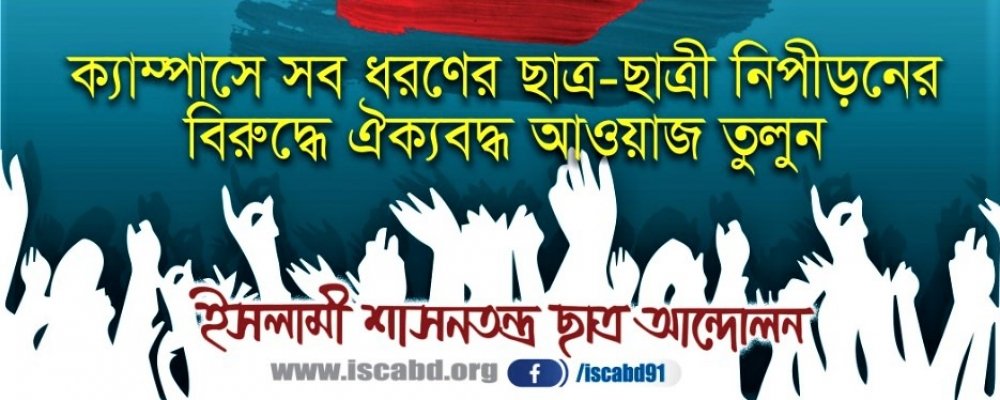


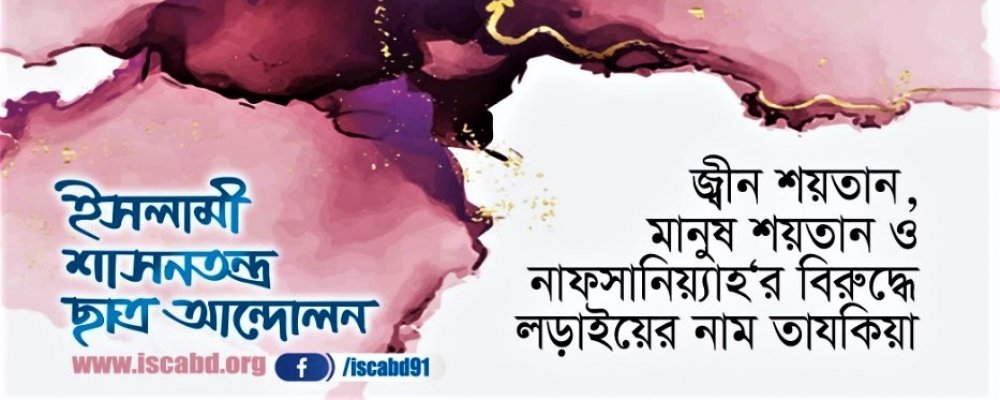






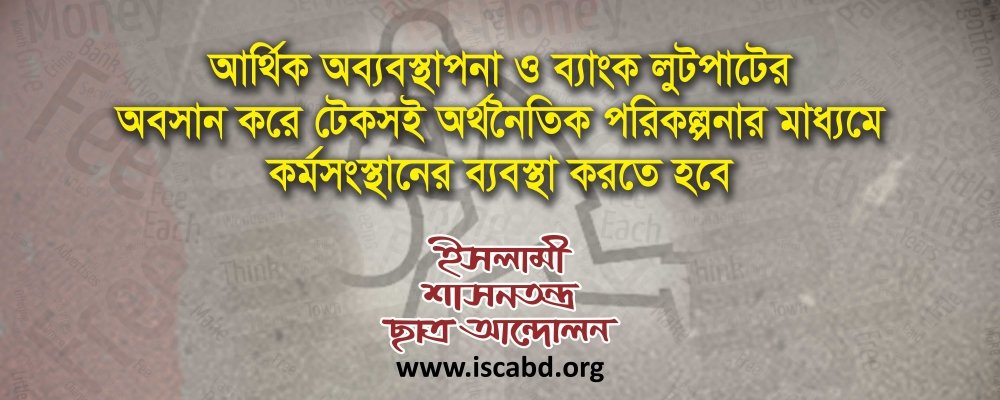



স্যোসাল লিংকসমূহ